সংবিধান ও নাগরিকদের গণতান্ত্রিক চেতনা, ইচ্ছা ও সংকল্প
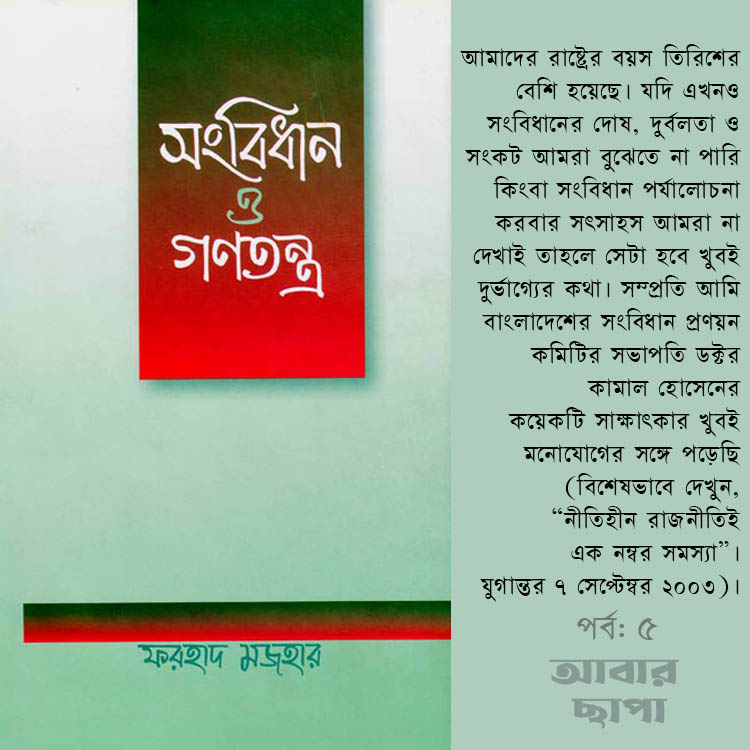
বিচারপতি সৈয়দ সাহিদুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন আইনজীবী সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার রোকনুদ্দিন মাহমুদ। প্রধান বিচারপতি কে এম হাসান বিষয়টি রাষ্ট্রপতির কাছে তুলেছেন বা আইনি ভাষায় ‘রেফারেন্স’ প্রেরণ করেছেন। তার মানে প্রধান বিচারপতি বা জুডিশিয়াল কাউন্সিল মনে করেছেন বিচার বিভাগের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বিষয়টি তদন্ত করে দেখা দরকার। রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি বা জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেলেও তদন্তের নির্দেশ দেবার এখতিয়ার রাখেন। খবরের কাগজে যখন আমরা দেখলাম যে, রাষ্ট্রপতি এই ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ চেয়েছেন তখন নাগরিক হিশাবে অনেক সাংবিধানিক এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আন্তরিক- অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ গঠন সংক্রান্ত গুরুতর প্রশ্ন এসে গেলো।
এটা আনন্দের কথা যে এই ধরনের গুরুতর বিষয়গুলো আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় নি। পেঁয়াজ নিয়ে সাম্প্রতিক রাজনীতির ডামাডোলেও হারায় নি। অন্তত দুইজন সাংবাদিক- বিশ্লেষক এই বিষয়ে লিখালেখি করছেন এবং কিছু প্রশ্ন নিয়ে তর্কও করছেন। শ্রদ্ধাভাজন এবিএম মূসা এবং অনুজ মিজানুর রহমান খান। ইতোমধ্যে তাঁরা একটা তর্কও জুড়ে দিয়েছেন। দেখুন, ‘সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের জেগে ওঠা মিজানুর রহমান খান (২৮ অক্টোবর ২০০৩), ‘রাষ্ট্রপতির সীমাবদ্ধতা বনাম বাধ্যবাধকতা’- এবিএম মূসা (২নভেম্বর ২০০৩) এবং ‘রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ভারসাম্যহীন’ মিজানুর রহমান খান (৪ নভেম্বর ২০০৩)।
আমরা তিন জন এর আগেও পরস্পরের সঙ্গে লিখিত তর্কবিতর্ক করেছি। করেছি সংবিধান নিয়েই। এবিএম মূসা বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন তিনি সংবিধান বিশেষজ্ঞ নন। আসলে আমরা কেউই নই। কিন্তু নাগরিক হিশাবে সাংবিধানিক বিষয় এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নাই। তাছাড়া সংবিধান শুধু উকিল-ব্যারিস্টাররা বুঝবেন, আমরা খালি তাঁদের কথা মতো চলব, সেই দিন অনেক আগেই ফুরিয়ে গিয়েছে। আমি অনেক সময় আমার লেখায় বলেছি বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের ভয়ানক দুর্বলতার প্রধান একটা কারণ হচ্ছে উকিল-ব্যারিস্টার দিয়ে সংবিধান মুসাবিদা করা। তাঁরা নানান দেশ থেকে সংবিধান টুকলিফাই বা নকল করেছেন এইচএসসি পরীক্ষায় নকল করে পরীক্ষা দেবার মতো। তবে তাঁরা তখনকার আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক স্বার্থ বহাল রাখবার ক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন মানতেই হবে। যেমন প্রধানমন্ত্রীর হাতে সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে রাষ্ট্রপতিকে অর্থহীন তৈরি করা। আদিবাসীদের স্বার্থ, আবেগ ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে একমাত্র ‘বাংলাভাষী’দের জন্য রাষ্ট্র কায়েম এবং সংবিধানে সম্পত্তির ধরন হিশাবে আদিবাসীদের যৌথ সম্পত্তিকে স্বীকার না করা– কাজে কাজেই বাংলাদেশকে বিচ্ছিন করবার পথ প্রশস্ত করা, ইত্যাদি। প্রমাণ নাই যে, শেখ মুজিবুর রহমান এই ধরনের সংবিধানই লিখতে বলেছিলেন। এমনকি নতুন সংবিধান সভা না ডেকে পাকিস্তানে সংসদের নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে সংবিধান রচনা বাংলাদেশের রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায় হিশাবেই ঐতিহাসিকরা বিবেচনা করেন এবং আগামী দিনগুলোতেও করবেন। কিন্তু দলীয় সংকীর্ণতা এবং ব্যক্তিস্তুতি কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল সেটা সেই সময়ের বাহ্যিক রাজনীতি দেখলে যেমন আমরা বুঝি, ঠিক তেমনি সংবিধান নিয়ে আলোচনা করলেও বহু কিছু বেরিয়ে আসে। যে-বিষয় নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে তার মধ্য দিয়েও আমরা আমাদের সংবিধান ও সাংবিধানির চিন্তার সংকটগুলো ধরতে পারছি।
আমি শ্রদ্ধাভাজন এবিএম মূসা কিম্বা মিজানুর রহমান খানের মতো বিনয়ের সঙ্গে কথা বলি না বলে অনেকে গোস্বা করেন। কিছু কথা চাঁচাছোলাভাবে না বললে চলে না। সংবিধান সেই রকমই একটা বিষয়। কারণ এর সঙ্গে আমাদের ভাগ্য এবং একটি জাতি বা রাষ্ট্র হিশাবে পৃথিবীর সভায় আমরা টিকে থাকব কি থাকব না সেই প্রশ্নও জড়িত। তাছাড়া আমি সংবিধানকে নিছক কাগজের বান্ডিল মনে করি না। এর সঙ্গে আমাদের চেতনা, ইচ্ছা ও সংকল্পের জীবন্ত সংযোগ ঘটানো জরুরি। অনেক সময় চাবুক দিয়ে না মারলে আমরা জাগি না। তবে স্বীকার করা উচিত যে পাঠকদের কাছে সাংবিধানিক বিষয়ে লেখালেখির সাড়াও এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি।
সংবিধানের মতো কঠিন বিষয় নিয়ে লেখালেখিকে তাঁরা খুবই গুরুত্ব দিয়ে পড়েন। রাষ্ট্রের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠনের দিকগুলো আমাদের রাজনৈতিক পর্যালোচনা ও কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু করে তুলতে পারলে কোনো বিশেষ দল বা বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দোষারোপ করবার প্রয়োজন পড়ে না। আমি মানি যে, ১৯৭২ সালে আমাদের রাজনৈতিক চেতনা এখনকার মতো প্রখর ছিল না, কিম্বা সংবিধানে নানা অনুচ্ছেদগুলোর আইনি, নির্বাহী বা বিচার বিভাগীয় তাৎপর্য পরিষ্কার ছিল না। সংবিধানের মর্মর্গত বিষয়ে আমাদের আগ্রহও প্রায় ছিল না বললেই চলে। মানবেন্দ্রনাথ লারমার আকুতিগুলো আমাদের কানে এসে না পৌঁছানোর কারণও হয়তো এখানে নিহিত। এটা একটা উদাহরণ। ভুল সংবিধান যে একটি রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন বা ধ্বংস করতে পারে সেই বোধ আমাদের হয়নি। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম আদিবাসীদের আমরা সংবিধানের জোরে ‘বাঙালী’ বানিয়ে ফেলতে পারব। নাগরিক হিশাবে আমরা সংবিধানকে একটা কালো কালিতে লেখা সরকারিভাবে প্রকাশিত বই ছাড়া বিশেষ কোনো মূল্য দিয়েছি কি? ইতোমধ্যে আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। এখন খোলামনে আলোচনা ও তর্কবিতর্কের সময়।
একটি কথা বলে রাখি। উকিল-ব্যরিস্টারদের দিয়ে মুসাবিদা করা সংবিধানের সমালোচনা আমি করব ঠিকই, একই সঙ্গে বেয়নেটের খোঁচায় সংবিধান বদলে দেবার রক্তাক্ত কাহিনীগুলোও অবশ্যই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলব যে, রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণভাবে নিজেকে কীভাবে সংবিধান, আইন, সংস্কৃতি ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক নীতি ও কর্মকাণ্ড দ্বারা পরিগঠনের সম্ভাবনা তৈরি করে এবং ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে সেই বিষয়ে আমাদের জাতিগত চিন্তা বা ধারণা অতিশয় দুর্বল। সংবিধান বা আইনের বিষয়ে এখনও নাগরিকরা উকিল-ব্যারিস্টারদেরই মুখাপেক্ষী। এর বিপরীতে আছে সশস্ত্রতার দম্ভ- অর্থাৎ সামরিক শাসন, সংবিধানহীনতা ও আইনশূন্যতা। রাষ্ট্র ও রাজনীতি উভয়ের জন্যই যা বিপজ্জনক। অন্যদিকে যাঁরা শুরুতে সংবিধান প্রণয়নে ভূমিকা রেখেছিলেন তাঁদের একতরফা সমালোচনাও জাতিগত সংবিধান চেতনার দিক থেকে অন্যায় বলে মনে করি। নাগরিক হিশাবে আমার মনে হয় সেই সময় আমাদের জাতিগত চেতনার সীমা অতোটুকুই ছিল। অন্য দেশের সংবিধান টুকলিফাই বা নকল না করে নিজেদের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্পের কোনো সাংবিধানিক রূপ খাড়া করবার তৌফিক ১৯৭২ সালে আমাদের ছিল না। ফলে যে অপরাধে ব্যক্তিকে আমরা দায়ী করি জাতি হিশাবে তার দায় আমাদের সকলেরই কমবেশি প্রাপ্য। জ্ঞান বা বুদ্ধি নিয়ে কারবার করি বলে তাই দায় দেশের নাগরিক হিশাবে আমার নিজের কাঁধে বহন করতে আপত্তি নাই। একমাত্র এই স্পিরিটেই সাংবিধানিক তর্কবিতর্ক সামনে এগুতে পারে। নইলে ব্যক্তি, দল গোষ্ঠী পরস্পরকে দোষারোপ করেই যাবে। আর মূল প্রশ্ন বাদ দিয়ে অর্থহীন তর্কেই আমরা লিপ্ত হবো। সামনে অগ্রসর হতে পারব না ।
আমাদের রাষ্ট্রের বয়স তিরিশের বেশি হয়েছে। যদি এখনও সংবিধানের দোষ, দুর্বলতা ও সংকট আমরা বুঝেতে না পারি কিংবা সংবিধান পর্যালোচনা করবার সৎসাহস আমরা না দেখাই তাহলে সেটা হবে খুবই দুর্ভাগ্যের কথা। সম্প্রতি আমি বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ডক্টর কামাল হোসেনের কয়েকটি সাক্ষাৎকার খুবই মনোযোগের সঙ্গে পড়েছি (বিশেষভাবে দেখুন, “নীতিহীন রাজনীতিই এক নম্বর সমস্যা”। যুগান্তর ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩)। যদিও তিনি রাজনীতিবিদদের নৈতিকতাকে রাজনীতির ‘একনম্বর’ সমস্যা বলে অতি সংকীর্ণ নীতিবাদী অবস্থান আঁকড়ে ধরেছেন অথচ তাঁরই হাত দিয়ে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ পরিগঠন ও বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক বলে আমি মনে করি। তিনি এখনও সেটা মানছেন না। সরল মনে এযাবতকালের অভিজ্ঞতার আলোকেও মানছেন না। তবুও লক্ষ্য করেছি অনেক সাংবিধানিক বিষয় যে নতুনভাবে পর্যালোচনা করা সরকার এবং অনেক কিছু নতুন ভাবাভাবির প্রয়োজন আছে সেটা তিনিও স্বীকার করেন। আমার আশা, তিনি আরও খোলা মনে সাহসের সঙ্গে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ও পর্যালোচনা নাগরিকদের জানাবেন। এতে দেশ ও দশ উপকৃত হবে। এই চর্চাগুলো করা গেলে এবং বদ্ধ ছিপিগুলো খুলে ফেলতে পারলে দলীয় রাজনীতি ও সংকীর্ণতা অতিক্রম করে আমরা আরো বিচক্ষণ জায়গায় পৌঁছাতে পারবো বলে আশা করা যায়।
আমার এই লেখাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিচারক সৈয়দ সাহিদুর রহমানকে কেন্দ্র করে যে- সাংবিধানিক প্রশ্ন উঠেছে তার গুরুত্ব পাঠকদের সামনে তুলে ধরা। লেখাগুলোর প্রতি পাঠকদের নজর আকর্ষণ করা। দ্বিতীয়ত, আমরা ব্যাপারগুলো ধরতে বা বুঝতে পারছি কিনা সেটা পরখ করে নেওয়া। তৃতীয়ত, সাংবিধানিক ভাবনা ও তর্ককে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ পরিগঠন সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা বাড়ে এবং রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের শর্ত তৈরির কাজে আমরা ইতিবাচক অবদান রাখতে পারি। গণতান্ত্রিক রূপান্তর সংস্কারের মধ্য দিয়ে নাকি বৈপ্লবিক কায়দায় হবে সেটা অবশ্য ভিন্ন বিতর্ক। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গঠনের সংকট ও সমস্যা নিয়ে কথা আমাদের বলতেই হবে। এটাই আমাদের উন্নতির প্রথম ও প্রধান রাস্তা।
এখানে আমি মিজানুর রহমান খানের তোলা একটি বিষয় নিয়ে শুধু লিখব। সরল মনে স্বীকার করে রাখতে চাই যে, এবি এম মূসা ঠিক কী বলতে চাইছেন আমি ধরতে পারি নি। আমার মাথা একটু মোটা আছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির কর্তব্য পালনে বাধ্যবাধকতা ও সীমাবদ্ধতা এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও উচ্চতম আদালতের অবস্থান নিয়ে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা তিনি মানছেন না কেন সেইটা ধরতে পারলাম না। আমি মিজানের অতিশয় মূল্যবান দুই কিস্তি লেখার মর্মের সঙ্গে একমত। তিনি পরিশ্রম করে অনেক তথ্য আমাদের জানিয়েছেন, এতে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি। তাঁর কথা তিনি যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। ফলে মতৈক্যের জায়গাটায় এখন না গিয়ে আগে ভিন্ন মতের জায়গাটা দিয়েই শুরু করি।
বিচার বিভাগ বিচারক সাহিদুর রহমানের ব্যাপারটি রাষ্ট্রপতিকে জানায়। যদিও রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলেই এই ব্যাপারে তদন্তের নির্দেশ দিতে পারতেন। তিনি দেন নি। বিচার বিভাগের কাছ থেকে রেফারেন্স পেয়ে রাষ্ট্রপতি বরং প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছেন অতিরিক্ত বিচারক সাহিদুর রহমানের বিষয়টি তদন্ত করা হবে কিনা। এই ঘটনাটি বাংলাদেশের সংবিধান ও ক্ষমতার চরিত্র সম্পর্কে ভাল একটি ইঙ্গিত দেয়। মিজানুর রহমান খান সঙ্গতভাবেই সেই ইঙ্গিত ধরে তর্কে প্রবেশ করেছেন। বলা বাহুল্য, অসৎ আর দুর্নীতিবাজ বিচারকের বিচার হতেই হবে এটা তর্কের বিষয় নয়। আইন বা বিধান থাকলেও নানান কারণে বিচার নাও হতে পারে সেটাও এখানে তর্কের বিষয় নয়। প্রশ্ন হচ্ছে- এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ আর বিচার বিভাগের সম্পর্ক কী? বিচারের নির্দেশ কে দেবে? বিচার কে করবে? কিভাবে করবে? অভিযুক্তের শাস্তি কে দেবে? ইত্যাদি। মিজানুর রহমান খান বলছেন, ‘কোন বিচারক, নির্বাচন কমিশনার, পিএসসি সদস্য ও সিএন্ডএজির বিরুদ্ধে কাউন্সিল তদন্ত শুরু করবে কিনা তার চূড়ান্ত সন্তুষ্টি সংবিধান প্রধান বিচারপতি বা প্রাধানমন্ত্রীকে নয় রাষ্ট্রপতিকেই দিয়েছে।’ মিজানুর রহমান খান সরাসরি নানান সাংবিধানিক বিধি-বিধান নিয়ে কথা তুলেছেন। ফলে সাধারণ পাঠকরা বোধহয় বিষয়টি উকিল-ব্যারিস্টারদের ব্যাপার বলে ভয়ে এড়িয়ে যেতে চাইবেন। সংবিধান কেন এতো গুরুতর হয়ে উঠল সেই দিকটা বোঝাবার জন্য কয়েকটি কথা বলা যাক ।
সৈয়দ সাহিদুর রহমানের নিয়োগ দিয়েছেন বর্তমান সরকার। বিচারকদের নিয়োগ একনায়কতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতার আনুমোদন ছাড়া হয় না। রাষ্ট্রের দিক থেকে দেখলে এই অনুমোদন আসে রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা বা প্রধানমন্ত্রীর তরফে। নিয়োগের ধরনটাই বিচারবিভাগকে রাজনৈতিক দলের বা রাষ্ট্রের দিক থেকে নির্বাহী বিভাগের অধীনস্থ করে।
দুর্নীতিবাজ বিচারকের শাস্তির প্রশ্নেও যদি প্রধানমন্ত্রীর ‘পরামর্শ’ প্রয়োজন হয় তাহলে এ কেমন বিচারব্যবস্থা? এ কেমন রাষ্ট্র? এটাই হচ্ছে নাগরিকদের প্রশ্ন। নাগরিকরা তর্ক করবেন যে, সংবিধান ও আইন তো সকলের জন্যই সমান হবার কথা? তাহলে কেউ দোষী কিনা সেই তদন্ত করতে গেলেও কেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ লাগবে?
এখানে নাগরিকরা প্রায় সবসময়ই ভুল করেন। তাঁদের ধারণা আইন, বিচার, ইনসাফ ইত্যাদি বুঝি হাওয়াই ব্যাপার। এটা আপনা আপনাতেই হয়ে যাবার কথা। যদি সংবিধান, আইন বা বিচার ব্যবস্থাটাই বিচার করবার বাধা হয়, যদি সংবিধান, আইন বা বিচার ব্যবস্থাই ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের প্রতিবন্ধক হয় তখন? মিজানুর রহমান খান ঠিক সেই প্রশ্নটাতেই যেতে চাইছেন। আমি তাঁর লেখা পড়ে নাগরিক হিশাবে এটা বুঝেছি যে, রাষ্ট্রপতি সৈয়দ সাহিদুর রহমান সম্পর্কে তদন্ত করবেন কিনা সেটা যদি তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে জেনে নিতে হয় তাহলে এটা গুরুতর সাংবিধানিক মুশকিল হয়ে হাজির হয়। যার মীমাংসা আমাদের রাজনৈতিকভাবে করতেই হবে। আমাদের সংবিধানের সংকটের প্রতিই এখানে নজর পড়েছে। অর্থাৎ এটা আমার ভাষায় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ পরিগঠনের সংকট। এই সংকটের প্রতি নজর না দিয়ে দুর্নীতিবাজ বিচারকের বিচারের ব্যাপার নিয়ে উত্তেজক রাজনীতি বাহ্যিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব হয়ে উঠতে পারে বড়োজোর, রাষ্ট্রের গণতন্ত্রায়নে কোন ভূমিকা রাখবে না। সংবিধানের সংস্কার বা বদল ছাড়া এই সমস্যার সমাধান হবে না। এই সংস্কার বা বদল যে দরকার এটাই মিজানুর রহমান খানের বক্তব্য। আমি তাঁর সঙ্গে একমত।
অতএব সংবিধান নিয়েই তার তর্ক। আসলেই এটা সংবিধান এবং কীভাবে আমরা সংবিধান ব্যাখ্যা করি তারই সংকট কিনা সেই বিচারে মিজানুর রহমান খান নেমেছেন। সংবিধান ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতির নিয়োগের দায়িত্ব ছাড়া রাষ্ট্রপতিকে কোনই ক্ষমতা দেয় নি বরং রাষ্ট্রপতিকে একজন প্রধানমন্ত্রীর অধীনস্থ করেছে। একজন প্রধানমন্ত্রী বা ব্যক্তির কথাটি খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী– মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেট নয়। যেহেতু সংবিধান বলছে যে, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন অতএব, রাষ্ট্রপতি বিচারক সৈয়দ সাহিদুর রহমানের বিষয় তদন্ত করতে চাইলেও প্রধানমন্ত্রীর ‘পরামর্শ’ ছাড়া সেটা করতে পারেন না। সংবিধান, দেখা যাচ্ছে, এই ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ বিচার বিভাগ সাংবিধানিকভাবেই প্রধানমন্ত্রীর অধীনস্থ হয়ে রয়েছে। বিচারককে যদি দলীয় স্বার্থে নিয়োগ দেওয়া হয়, তহলে তার দুর্নীতির তদন্ত প্রধানমন্ত্রী করতে দেবেন কিনা সেই সন্দেহ উঠেছে। সাংবিধানিক প্রধান হিশাবে এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির কিছুই করার নাই।
কিন্তু মিজানুর রহমান খান ৪৮ (৩) অনুচ্ছেদের শর্ত নিয়ে ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শর্ত হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ রাষ্ট্রপতি নেবেন ঠিকই কিন্তু ‘প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে কোন পরামর্শ দান করিয়াছেন কিনা এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করিতে পারিবে না।’ মজার কথা। মজার সংবিধান!
মিজানুর বলছেন, যাঁরা ৪৮ (৩) সংবিধানের আংশিক পাঠ করে রাষ্ট্রপতিকে ঠুঁটো জগন্নাথ ধরে নিয়েছেন তাঁরা শর্তের দিকটা উপেক্ষা করছেন। তিনি বলছেন, ‘এই শর্ত দেয়াই হয়েছে রাষ্ট্রপতি যাতে ক্ষেত্রবিশেষে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়াই চলতে পারেন তার রক্ষাকবচ হিশাবে’।
আমি বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে ঠুঁটো জগন্নাথ বা আরও লোকায়ত ভাষায় কলাগাছই মনে করি। তিনি সাংবিধানিক প্রধান এই কথাটির যে-তাৎপর্য আমরা অন্যান্য দেশের সংবিধানে দেখি বাংলাদেশের সংবিধানে তেমন দেখি না। যে বিষয় মিজানুর রহমান খান নিজেও কিছুটা আলোচনা করেছেন কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যা আমাকে ভাবিয়েছে। মিজানুর কেন রাষ্ট্রপতিকে ‘রক্ষাকবচ’ দিতে চাইছেন সেটা আমি ধরতে পেরেছি বোধহয়। বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে কলাগাছ গণ্য করারও বিপদ আছে। অতএব, ভিন্ন ব্যাখ্যা খাড়া করে তাঁর হাতে রক্ষাকবচ ধরিয়ে দিয়ে সৈয়দ সাহিদুর রহমানের মতো বিষয়গুলো হ্যান্ডেল করবার একটা সুযোগ করিয়ে দিতে পারলে মন্দ হয় না। এই জন্যই কি রক্ষাকবচ ধরিয়ে দেবার প্রয়োজনীয়তা? কিন্তু কথা আছে।
এক. সংবিধান পরিষ্কারই প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতির নিয়োগ ছাড়া রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর অধীনস্থ করেছে।
দুই. সংযুক্ত শর্ত কোনভাবেই পরামর্শ না করার সুযোগ দেয় নি। রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই পরামর্শ করতে হবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আদৌ কোন পরামর্শ দিলেন কিনা কিম্বা দিয়ে থাকলে কী পরামর্শ দিয়েছেন শুধু সেটাই আমরা আদালতে গিয়ে জানতে চাইতে পারবো না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি পরামর্শের প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে নিজে কোন সার্বভৌম সিদ্ধান্ত নেবেন সেই ক্ষমতা সংবিধান তাকে দেয় নি। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে কোন বিষয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দিচ্ছেন কি দিচ্ছেন না সেটা একান্তই প্রধানমন্ত্রীর এখতিয়ার রাষ্ট্রপতির নয়।
তিন. যদি আমরা রাষ্ট্রপতির কোন সার্বভৌম এখতিয়ার মানি তাহলে আমরা নির্বাহী ক্ষমতাকে দুই ভাগে ভাগ করার কথা বলছি। একাংশ প্রধানমন্ত্রীর আর আরেকাংশ রাষ্ট্রপতির হাতে থাকছে । তাহলে প্রশ্ন উঠবে রাষ্ট্রপতি কি নির্বাহী বিভাগের অংশ, নাকি তিনি সাংবিধানিক প্রধান? সাংবিধানিক প্রধানের হাতে আংশিক নির্বাহী ক্ষমতা প্রদানের বিস্তর মুশকিল আছে। ঠিক তেমনি নির্বাহী প্রধানের হাতেও আমরা সাংবিধানিক ক্ষমতা দিতে পারি না। সেটা একান্তই বিচার বিভাগের এখতিয়ার। সেই ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি বা জুডিশিয়াল কাউন্সিল যদি সাংবিধানিক প্রধান হিশাবে কোন বিষয় রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করে, সেটা ঠিকই আছে। ঠিক তেমনি, ‘প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করিবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করিলে যে কোন বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করিবেন’ [দেখুন সংবিধান ৪৮ (৫)]।
চার. আমরা নির্বাহী ক্ষমতা এবং সাংবিধানিক ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য করছি না। প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্রপতির নির্বাহী ক্ষমতা না থাকতে পারে, তাতে সংবিধানে দোষের কিছু নাই। রাষ্ট্রপতিকে সেই ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নই। কিন্তু ‘রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন’ কথাটির মানে কী? অর্থাৎ কার্যক্ষেত্রে এর অভিপ্রকাশটা কেমন? তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে অভিবাদন নিয়েই খালাস আর অন্য দেশের দূতদের পরিচয়পত্র নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন? নাকি ‘রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে থাকা’ মানে তাঁকে সুনির্দিষ্টভাবে এমন কিছু সাংবিধানিক ক্ষমতা দেওয়া যার প্রয়োগ তাঁর মাধ্যমেই হবে এবং সেই ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ হবে তাঁর ক্ষমতা কার্যকর করবার অঙ্গ। ঠিক এখানেই সংবিধানের চরিত্রটা ধরা পড়ে।
সহজে বুঝতে পারব যদি প্রশ্ন করি যে, প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ ওঠে তাহলে তদন্ত করবে কে? এটাও কি রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে করতে হবে? প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ ওঠে তাহলে সেটা তদন্ত করবার অধিকারী বা কে? তিনি কেমন করে সেটা করবেন? প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় বিষয় রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করবেন। ঠিকই আছে। কিন্তু অবহিত হয়ে থাকাই কি যথেষ্ট? যদি প্রধানমন্ত্রীর কোন রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড বা পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নির্ণয় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কিম্বা বাংলাদেশের সংবিধানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহলে তার বিচার কে করবে? তাঁর অনুরোধে প্রধানমন্ত্রী যে কোন বিষয় তাঁরই তৈরি ইয়েসম্যান মন্ত্রিসভায় আলোচনা করলে তো চলবে না ।
পাঁচ. তার মানে আমরা এমন এক সংবিধান চাই যেখানে প্রধানমন্ত্রীকে ‘ইমপিচ’ করা যায়। দেশদ্রোহিতার দায়ে বিচার করা যায়। অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, অর্থনীতি ও আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিতে বিশৃংখলা ও অরাজকতা সৃষ্টির জন্য প্রধানমন্ত্রীকে দায়ী, দোষী ও বিচার করবার সাংবিধানিক সুযোগ অবশ্যই থাকতে হবে। রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধান হিশাবে প্রধানমন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে চুক্তি করছেন, ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক করছেন সেটা বাংলাদেশের শত্রুমিত্র প্রশ্ন ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা সেই প্রশ্ন আমরা কোথায় তুলব? কিম্বা আমাদের পক্ষে কে সেটা আগে খেয়াল করবেন? রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে বিরাজমান রাষ্ট্রপতি নয় কি? রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধানের বিচার কিম্বা তাঁর কর্মকাণ্ড সংবিধানসম্মত কিনা সেই নিয়মিত নিরীক্ষার কোন সুযোগ নাই বলে এবং আরও বহু দোষের কারণে এই সংবিধান শুরু থেকেই অর্থাৎ ১৯৭২ সাল থেকেই অগণতান্ত্রিক, গণবিরোধী, সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্নে ধর্মীয় বিধানের ছুতা তুলে নারীকে বঞ্চিত করবার দলিল এবং সর্বোপরি সংসদীয় পদ্ধতির নামে মূলত প্রধানমন্ত্রীর হাতে কেন্দ্রীভূত একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থারই একটা জগাখিচুড়ি দাসখত ছাড়া আর কিছুই নয়।
বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে সংবিধান। রাষ্ট্র ও রাজনীতির প্রাণ ভোমরা এই দলিলটির মধ্যেই নিহিত থাকে। একটি সংবিধান কাগুজে হয়ে যায় যদি তার সঙ্গে আমাদের প্রাণের কোন যোগ না থাকে। যতদিন নাগরিকরা নিজেরা সংবিধান পড়ে এই সংবিধান তাঁদের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা সেই বিচারে না নামছেন ততোদিন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিকাশ অসম্ভব। যতোদিন একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রয়োজনে প্রাণ দেবার জন্য নাগরিকরা প্রস্তুত না হবেন ততোদিন আমাদের দুর্দশারও শেষ হবে না। কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা সরকার ব্যবস্থা কায়েমও অসম্ভব।
দেখা যাচ্ছে নিছকই একজন বিচারকের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগের তদন্তের বিষয় ভাবলে আমরা সৈয়দ সাহিদুর রহমানের ব্যাপারটির কিছুই বুঝব না। এটা সরসারি সংবিধান এবং সংবিধানের সঙ্গে আমাদের চেতনা, ইচ্ছা ও সংকল্পের সম্পর্কের মামলা। গুরুতর বিষয়।
২২ কার্তিক ১৪১০। ৬ নভেম্বর ২০০৩, শ্যামলী।